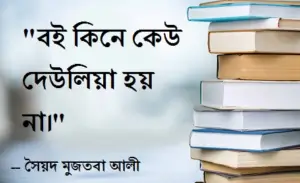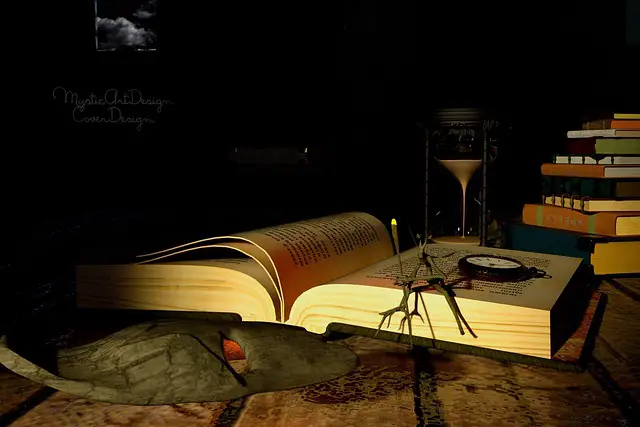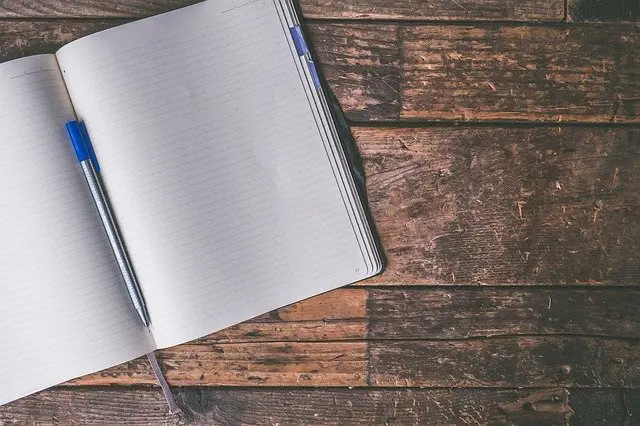বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ লেখা হয়েছে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দির মধ্যে। এই সময়ে বাংলায় পাল রাজাদের রাজত্ব ছিল। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। চর্যাপদের কবিরা এই সময়ে চর্যাগুলো রচনা করেছিলেন।
চর্যাপদের পদকর্তাদের নাম
চর্যাপদের পদকর্তাদের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। সুকুমার সেনের মতে ২৪ জন এবং ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে ২৩ জন পদ রচয়িতা চর্যাপদ রচনা করেছিলেন। পদকর্তাদের নামগুলো হচ্ছে-
লুই, কুক্কুরি, বিরুয়া, গুগুরি, চাটিল, ভুসুকু, কাহ্ন, কাম্বলাম্বর, ডোম্বি, শান্তি, মহিত্তা, বীণা, সরহ, শবর, আজদেব, ঢেন্টন, দারিক, ভাদে, তাড়ক, কঙ্কন, জঅনন্দী, ধাম, তান্তি, লাড়িডোম্বী।
পদ রচয়িতাদের নামের শেষে পা বা, পাদ যুক্ত করে লেখা হত। অনেক জায়গায় কুক্কুরিপা, কাহ্নপাদ এগুলো লেখা দেখবেন। যারা পদ রচনা করেন তাদের নামের শেষ পাদ বা, পা যুক্ত করা হয়। এগুলো রচনা করেছিলেন বৌদ্ধ সহজিয়ারা।
ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটি মোটা বই ODBL- Origin and Development of Bengali Language লিখে প্রমাণ করেছেন চর্যা আসলে বাংলা ভাষার সম্পত্তি, মোটেও অন্য ভাষার নয়। এটিকে বাংলার প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে সবাই এখন মেনে নেয়।
বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে ঐ সময়ের মানুষের সমাজচিত্র, ধর্মমত, সাধনতত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাদের লেখা পদগুলো থেকেই এইসব ধারণার উৎপত্তি।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম গদ্যরচনা শুরু করেছিলেন। চর্যাপদের সময় থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ছিল পদ্যের যুগ।
চর্যাপদে নিম্নবর্গীয় মানুষের পরিচয়
চর্যাপদের সময়ে নিম্নবর্গীয় মানুষ বা, অন্তজশ্রেণী বলতে যাদের বোঝানো হত তাদের অনেকের অস্তিত্ব এখনো আছে। এরা হচ্ছে- ডোম, চন্ডাল, মুচি, কামলি, ব্যাধ, জেলে, ধুনুরি, তাতি, পতিতা ইত্যাদি। ঐ সময়ের গানের বর্ণনায় ১৫ টি রাগের পরিচয় পাওয়া যায়।
দেখতে পারেন- চন্ডাল কাকে বলে?
স্বামী বিবেকানন্দ চাইতেন চন্ডালদের ব্রাহ্মণের মর্জাদায় উন্নীত করতে।
ভুসুকুপা নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দেয়ার সময় চন্ডালের কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে-
আজি ভুসুক বাঙালি ভইলি, ণিঅ ঘরণি চন্ডালে লেলি
এরকম অন্যান্য পদকর্তারাও তাদের পদগুলোর মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন পরিস্থিতি ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের রচিত কাব্যের মাধ্যমে।
চর্যাপদের রচয়িতাদের ধর্মমত
পাল রাজবংশের পর সেন রাজবংশের শাসন শুরু হয়। সেন রাজারা রাজধর্ম হিসেবে হিন্দু ধর্মের প্রচলন করেন। অনেকে মনে করেন এই সময়ে হিন্দু রাজাদের কেউ ধর্মের মাঝে জাতপাতের ধারণা প্রচলন করেছেন। যাইহোক, চর্যাপদের রচয়িতারা ছিলে সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য।
এই সময়ে চর্যাপদের রচয়িতারা জীবন বাচাতে পালিয়ে নেপালে যান। এই কারণেই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগারে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন খুজে পান।
তিনি ‘ডাকার্ণব’ ও ‘দোহাকোষ’ ও খুজে পেয়েছিলেন। এই তিনটি বই ১৯১৬ সালে ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা’ নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়।
চর্যাপদের সমাজচিত্র
বৌদ্ধ সহজিয়ারা ছিলেন আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলা মানুষ, তারা লিখতেনও নিজেদের ভাষায়। উচু শ্রেণীর লেখার ভাষায় তারা লিখতেন না বলেই কালক্রমে আমরা আজকে বাংলা ভাষা পেয়েছি। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ সবচেয়ে বেশী। এছাড়া দেশী, বিদেশী, তদ্ভব ও অর্ধ তৎসম শব্দ এখন বাংলা ভাষার সম্পদ।
তৎকালীন সময়ের সমাজচিত্র অঙ্কন করা পদকর্তাদের উদ্দেশ্য ছিল না, তাদের উদ্দেশ্য ছিল গুপ্ত সাধনা পদ্ধতির বর্ণনা করা। সহজিয়া সাধক সম্প্রদায়ের সেই লেখাগুলোতে তথাপিও ঐ সময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে।
ক্ষুধা, দারিদ্র, আক্ষেপ, বেদনা, প্রেম, দ্রোহ, অনিয়ম, অত্যাচার, প্রকৃতি সব মিলিয়ে বাস্তব জীবনের চিত্রই মূর্ত হয়ে ওঠে। চর্যায় দেখা যায় নারী সৌন্দর্য্যের বর্ণনা-
উঞ্চা উঞ্চা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরাঙ্গ পীচ্ছ পরিহাণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥
সরলার্থঃ উচুঁ উচুঁ পর্বত,সেখানে বাস করে সবরী বালি(বালিকা)। ময়ূরের পুচ্ছ পরিধান করে সবরী, গলায় গুঞ্জরী মালি(মালা)।’
আরো পাওয়া যায়-
টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥
বেঙ্গসঁ সাপ চঢ়িল জাই।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামাই ॥
বলদ বিআএল গবি আ বাঁঝে।
পীঢ়া দুহিঅই এ তীনি সাঝে ॥
জো সো বুধী সোহি নিবুধী।
জো সো চোর সোহি সাধী ॥
নিতি নিতি সিআলা সিহে সম জুঝই।
ঢেণ্টণ পাএর গীত বিরলে বুঝই ॥
সরলার্থঃ ‘বস্তিতে আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, (অথচ) প্রেমিক (ভিড় করে)। ব্যাঙ কর্তৃক সাপ আক্রান্ত হয়। দোয়ানো দুধ কি বাঁটে প্রবেশ করে? বলদ প্রসব করল, গাই বন্ধ্যা, পাত্র ভরে তাকে দোয়ানো হল এ তিন সন্ধ্যা। যে বুদ্ধিমান, সেই নির্বোধ, যে চোর সেই সাধু। নিত্য নিত্য শৃগাল যুদ্ধ করে সিংহের সাথে। ঢেণ্টণপাদের গীত অল্পলোকেই বুঝে।
নৌকা, গরু, পাহাড় ইত্যাদি নানা বিষয় তাদের কবিতায় উঠে আসে। চর্যাপদ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং কাজ করেছেন ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড.মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ড. প্রবোধকুমার বাগচী এবং আরো অনেক বিদগ্ধজনেরা।
আরো পড়তে পারেন-